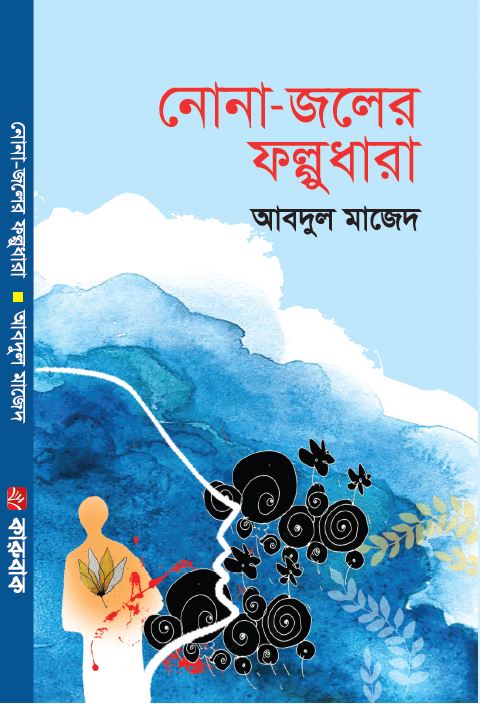ফাল্গুন মাসের শুক্ল পক্ষ।
সূর্য ডুবতে না ডুবতেই বিবর্ণ চাঁদ ধীরে ধীরে সোনালি রঙে নেয়ে আস্তে আস্তে রূপালি জ্যোছনা ছড়িয়ে দিতে লাগলো বৃক্ষরাজির গাঢ় সবুজের চাঁদোয়ার উপরে। একটু পরেই সাপের মত একেবেঁকে বয়ে চলা মুক্তেশ্বরীর ঢেউয়ে ঝিরিঝিরি বাতাসে তোলা ঢেউয়ের বুকে দেখা যাবে চাঁদের আলোর ঝিকিমিকি নাচ।
অন্ধকার গাঢ় হওয়ার আগেই আমিও মুক্তেশ্বরীর তীর ঘেঁসে বেতঝাড়, নাটাবন আর বাঁশ বাগানের ভিতর দিয়ে ঘাস-লতা-পাতায় ঘেরা পায়েচলা পথ ধরে হাজির হলাম বাথানবাড়ি মহাশ্মশানের পাশে আমাদের খেজুর বাগানে। ঠিক এ সময়টাতেই গাঁয়ের ছেলেরা পাটকাঠির নল হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে রস খেতে। রস চুরি। আমাদের কৈশোরে তখনও খেজুরের রস মহার্ঘ না হওয়ার কারণে গ্রামের ছেলেরা রস চুরি করে খাওয়াকে একটা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হিসেবে মনে করতে।
তখন ফাল্গুন মাসের শেষ পর্যন্ত খেজুর গাছ কাটা হতো। ফাল্গুন মাসে মাটির স্যাঁতসেতে ভাবটা কমে আসায় খেজুরগাছে রসের পরিমাণ কমে আসত। রসে পানির পরিমাণ কম হওয়ায় রস কম হলেও চিনির পরিমাণ বেশি থাকত বলে রস খুবই মিষ্টি হতো। আবহাওয়া গরম থাকায় সকালে এ রস বেশিক্ষণ ভাল থাকত না, তাই এ সময়ের সান্ধ্যরস খুবই জনপ্রিয়।
চক্রবর্তীদের নিকট থেকে যখন এ খেজুর বাগান কেনা হয় তখন প্রায় সমস্ত জমি জুড়ে শিয়ালকাঁটার ঘন ঝোপে পরিকীর্ণ থাকত। কার্তিক মাসে জমি চষে যখন সরষে বা মসুর বোনা হতো, কাঁটা-ঝেপের নামনিশানাও থাকত না। ফসল পেকে উঠতে না উঠতে পুরো জমি শিয়ালকাঁটা ঝোপে ভরে উঠত। যে সব নিচু জমিতে আমন ধানের চাষ করা হয় সেখানে শিয়াল কাঁটা জন্মে না। কিন্তু তার পাশের উঁচু জমিতেই শিয়ালকাঁটায় ছেয়ে যেতো। সম্ভবত পাঁক কাদায় শিয়াল কাঁটার বীজ অথবা শিকড় পচে যেতো, তাই নিচু জমিতে শিয়াল কাটা জন্মাত না। ভেবে চিন্তে বুদ্ধি করে জমি থেকে ছয় ইঞ্চি পরিমাণ মাটি কেটে ফেলে দেয়ার পরে জমিটাকে শিয়ালকাঁটা মুক্ত করা গেছে। আউস ধান কিংবা পাট চাষ করা হতো, রবিশস্য মৌসুমে সরষে কিংবা মসুর চাষ করা হতো। জমিতে থাকা পনের থেকে কুড়িটা খেজুরগাছ ছিল। আব্বা সেগুলো খুব যত্ন করে কাটতেন। আমার কাজ ছিল সন্ধ্যা হলেই রস পাহারা দেয়া রাত নয়টা দশটা পর্য়ন্ত। এর পরে সাধারণত রস-চোর ছেলেদের দৌরাত্ম খুব একটা দেখা যেতো না।
আমি তেমন দুরন্ত কিংবা ডানপিঠে ধরনের না হলেও ভূতের ভয় তেমন পেতাম না। আরো ছোটো বেলায় প্রাইমারি স্কুলে থাকতে রাতের অন্ধকারে একা চলেছি ভূতের ভয়ে আত্মাটাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে। এখন ভয় একটু কমে এলেও মাঝেমাঝে মাথায় ভূত চেপে বসে।
একটি সম্মিলিত কান্ডের উপর বেড়ে ওঠা শ্মাশানের বিশালাকায় অশ্বত্থ, বট ও আমগাছের জটিল মিশ্রণটি আমাদের খেজুরবাগান থেকে মাত্র একশত গজ উত্তরে। দুয়েকটি বেয়াড়া ডাল মুক্তেশ্বরী ডিঙিয়ে ওপারে পান্তাপাড়ার মাটিতে ঝুরি নামিয়ে দেয়ার মত ঔদ্ধত্য দেখাতে শুরু করেছে।
পরপর বেশ কয়েকজন সাধুকে বটগাছের গোড়ার আস্তানা গাড়তে দেখিছি। রাতের বিভিন্ন প্রহরে তাদের শিঙা ফুকার শব্দ এখান থেকে প্রায় এক কিলোমিটার ভাটিতে আমাদের বাড়ি থেকে শোনা যেতো। এরা দিনের বেলা গেরুয়া বসন পরে বাড়িবাড়ি গিয়ে করতাল বাজিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষে করে বেড়াত। গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায় এ সকল কথিত সাধুসন্তদের বেশ ভক্তি করত এবং চালটা, কলাটা, মুলোটা দিত। কেউকেউ অবশ্য এদেরকে ফেরারি আসামী কিংবা গুপ্তচর হিসেবে সন্দেহের চোখে দেখত। এদের কেউ-ই খুব বেশিদিন স্থায়ী হতো না। বেশকিছুদিন একাধারে থাকার পরে এরা গেঁয়ো যোগীতে পরিণত হতো, তাই ভিক্ষের পরিমাণ কমে আসত; অথবা তাদের পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ার আশংকায় একদিন কাউকে কিছু না বলে হুট করে উধাও হয়ে যেত।
শ্মশানের বটতলাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। বিশেষ করে পুজোর মওসুমে এখানে যাত্রাপালা, নাচ-গান অনুষ্ঠিত হতো। সে জন্য এখানে একটা শান-বাঁধানো বেদীও ছিল। নানা ধরণের ভয়ংকর সব ভূতুড়ে কাহিনীও শোনা যেত এই শ্মশানকে ঘিরে। সবথেকে ভয়ংকর যে কাহিনীগুলো যার মুখে শুনতাম তার নামটা আজ মনে নেই। তার আদি নিবাস নোয়াখালী। বহুদিন হলো কাছেই একটি গ্রামে আস্তানা গেড়েছে। এক সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ছিল। খেমকারান সেক্টরে ১৯৬৫ সালে যুদ্ধও করেছিল বলে তার মুখ থেকেই শুনেছি। উচ্চতায় সাড়ে ছয়ফুটের কম নয়। উচ্চতার সাথে মিলিয়ে তার সুঠাম দেহটা যে এককালে বিশালাকায় ছিল সেটা অনুমান করা কঠিন নয়। দারিদ্রেরে কষাঘাতে জর্জরিত। তার কাজ ছিল বিভিন্ন জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করা। এই কাঠ সে বিক্রি করত না কি তার বাড়িতে রান্নার কাজে লাগাতো তা জানি না। তবে তার জীর্ণ বস্ত্র ও ভগ্ন স্বাস্থ্য দেখে বুঝতাম যে, তার বাড়িতে এমন কিছু মেজবান চড়ত না যে তার জন্য এত কাঠ প্রয়োজন হবে।
এই লোকটিই যে ভঙ্গিতে শ্মশানের ভয়ংকর জন্তু-জানোয়ার আর অশরীরী জীবের গল্প শোনাত তাতে আমরা রোমঞ্চিত ও সন্ত্রস্ত না হয়ে পারতাম না। একদিন তো বলল, সে শ্মশানঘাটে বসে থাকা অবস্থায় দিনেদুপুরেই অদৃশ্য কেউ একজন তাকে আড়-কোলা করে ধরে শূন্যে ভাসিয়ে নদীর ওপারে পান্তাপাড়ার মাটিতে ছেড়ে আসে। দিনের বেলা তার এ গল্পগুলোকে গাঁজাখুরি মনে হলেও রাতের অন্ধকার নামার সাথে সাথে গল্পগুলো ভূতের মতই ভয়াবহ হয়ে মাথায় চেপে বসত।
তার এ সব গল্পের একটা ব্যাখ্যাও দাঁড় করিয়েছিলাম। যেহেতু বাথানবাড়ি মহাশ্মশানের গাছটি বিশাল, তাই এখানে শুকনো জ্বালানিকাঠও পাওয়া যেতো প্রচুর। হিন্দুরা এ গাছকে পবিত্র মনে করে বিধায় তারা এ কাঠ পোড়াত না। কিন্তু মুসলমানেরা এখান থেকে কাঠ সংগ্রহ করত। কাঠের রাজ্যে একাধিপত্য যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেজন্যই লোকটা শ্মশানের এই বটগাছকে কেন্দ্র করে নানারঙের ভূতুড়ে গল্প ফাঁদত।
যাইহোক, অন্ধকার রাত আর জ্যোছনা রাতের রূপ ও প্রকৃতি ভিন্ন। অন্ধকার রাতে পথের দুধারের ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গলের ভিতর জোনাকীর আলো ছাড়া কিছু দেখা যেতো না। নিজের পায়ের খুব কাছেই সাপ থাকলেও সেটা চোখে দেখা যেতো না, তাই মনে নানা ধরণের শংকা উঁকি দিলেও একপ্রকার নির্ঝঞ্ঝাটে পথ চলা যায়। বিপত্তি দেখা দেয় জঙ্গল কিংবা ফাঁকা মাঠে জ্যোছনা রাতের আলো-আঁধারিতে পথ চলতে গিয়ে। পাতায় পাতায় আলো ছায়ার নাচন চোখের সামনে ও মনের কোনে নানা রকম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করত। আট/দশফুট দূরে মাটিতে পড়ে থাকা একটা ডালকে যে কতবার সর্প-ভ্রমে পিছিয়ে এসে পাশের কোনো বাড়িতে গিয়ে হারিকেন ও লাঠি নিয়ে এসে শেষ পর্য়ন্ত দেখতে পেয়েছি ওই বস্তুটি আসলে একটা শুকনো ডাল।
খেজুরের রস পাহারা দিতে দিতে লক্ষ্য করলাম পশ্চিম দিকের পাকা রাস্তা থেকে কে যেন মাঠের ভিতর নেমে এলো। কাছে আসতেই দেখতে পেলাম চাদর গায়ে দিয়ে এগিয়ে আসছে দেবু। আমাদেরই গ্রামের, আমার বন্ধু। বুঝলাম চাদরের নিচে তার অস্ত্রটা লুকানো আছে, অর্থাৎ ভাড় থেকে রস খাওয়ার জন্য পাঠকাঠির নল। সব সময় যে গাছে উঠে রস খেতে নল লাগে তা নয়। এক পা খেজুর গাছের সুবিধামত একটা খাঁজে রেখে আরেক পা দিয়ে খেজুরগাছ আঁকড়ে ধরে গাছ থেকে ভাড় খসিয়ে দুহাতে ভাড় ধরে ভাড়ের কানায় মুখ লাগিয়ে রস চুমুক দিয়ে খাওয়া এক আশ্চর্য় দক্ষতার বিষয়। আমি যেহেতু উপস্থিত ছিলাম তাই সে আমার গাছে রস খাবে না সেটা জানা কথা। না থাকলে কি হতো সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তার সাথে গল্প করতে করতে আমাদের জমির পাশের জমি অর্থাৎ দুখিরামের জমিতে গেলাম। সেখানেও দুখিরামের গাছে ভাড় বাঁধা আছে। দেবু তরতর করে গাছে উঠে গেল। অবাক হয়ে দেখলো যে ভাড় ভরা। না এই ফাল্গুন মাসের টানের সময় রাত আটটার ভিতরে বিকালে কাটা গাছের ভাড় ভরবে না। দুখিরামের গাছ কাটা ছিল তিনদিন আগে। যে রাতে গাছ কেটেছিল সে রাতেই বৃষ্টি হয়। এ জন্য দুখিরাম রস সংগ্রহের জন্য ভাড়গুলো খোলেনি। পানিভরা ভাড় দেখে দেবুর মেজাজ গেল বিগড়ে। সে গাছ থেকে ভাড় খসিয়ে নিচে ফেল দিল। ভাড়টা ভিজে মাটিতে পড়ে আস্তে করে শব্দ করে ভেঙে গেল।
এখনো বেশ শীত। তাই মনে একটু সাহস আছে যে, সাপগুলো এখনো শীতনিদ্রা ছেড়ে মাটির উপরে উঠে আসেনি। আশে পাশের অধিকাংশ জমিই পতিত জমি। আশ-শেওড়া, ভাঁটফুল, উলুঘাস, নলখাগড়ায় ভর্তি। সাপের বসবাসের জন্য আদর্শ জায়গা। এখানে দিনের বেলা যখন আসি তখন গরমকালেও কখনো জ্যান্ত সাপ চোখে পড়েনি। তবে মাঝেমাঝেই চোখে পড়ত সাপের খোলস। সাপের খোলসগুলো লাঠি দিয়ে টান টান করে মেলে ধরে দেখেছি আট-দশ হাত লম্বা হবে এবং মাঝারি আকারের বাঁশের সমান মোটা। ধোঁয়া থাকলেই যেমন আগুন থাকবেই, তেমনি সাপের খোলস দেখলেই বুঝতে হবে খুব কাছেই সাপের অস্তিত্ব আছে। তবুও ভালো এখনো বেশ ঠান্ডা, তার উপর দুদিন আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে।
দেবু চলে যাওয়ার পর সাপের ভয় এবং ভুতের ভয়-দুইই আমার মনের জানালা ঠেলে আস্তে আস্তে ঢুকে পড়তে চাইছে। ঠান্ডা বেশি না। তবুও যেটুকু ঠান্ডা আছে, তা হাড়ে গিয়ে কামড় দেয়। বসন্তের হাওয়া এখনো মনস্থির করতে পারেনি সে কোন দিক দিয়ে প্রবাহিত হবে। হঠাত করেই শ্মাশানের দিকে চোখ গেলো। আমাদের জমির সীমানা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে শ্মশানঘাটের বটতলায় যাওয়ার জন্য পায়ে চলা পথ। ঐ পথের পাশে কে যেন হাতছানি দিয়ে আমোকে ডাকছে। জ্যোছনা রাত হলেও সবকিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। এটা বুঝতে পারছি একটা হাতের পাঞ্জা একবার আমার দিকে এগিয়ে আসছে আবার পিছিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হাতটা কি শূন্যে ভেসে আছে? কোনো ধড় কিংবা মাথা কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।
হঠাৎ করেই মাথা থেকে সব বিজ্ঞান সব যুক্তি কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। এখন মনে হচ্ছে এটা শ্মশান এবং এখানে শবদাহ করা হয়, মড়া পোড়ানো হয়। এখানে স্থায়ী কোন ক্রিমেটরি বা চিতা নেই। নদীর ঢালে যত্রতত্র শবদাহ হয়ে থাকে। শিশুমৃত্যু কিংবা অপঘাতে মৃত্যুজনিত লাশগুলো পুতে ফেলা হয়। এদেরই কারো বিদেহী অতৃপ্ত আত্মা কি আমাকে ডাকছে? হয়ত তার জাগতিক চেহারাটা ধারণ করতে পারছে না। তাই আলো-আাঁধারিতে কোনো রকমে একটা হাতকে পুনর্গঠিত করে তার ইশারায় আমাকে শ্মশান ঘাটে ডেকে নিয়ে গিয়ে কাদার ভিতরে গেড়ে দিতে চায়।
গো-ভূতের কথা শুনেছি। গরুকে যখন ভূতে ধরে তখন ভূত গরুর মাথাটা ক্ষেতের আলের পাশে সজোরে গেড়ে দেয়। এমন গরুকে উদ্ধার করতেও দেখেছি। আলের ধারে গরুর মাথা গেড়ে দেয়ার ফলে যে গর্তের সৃষ্টি হয় তাও দেখেছি। একটা গরুকে তো নদীর ধারেই কাদা-পানিতেই গেড়ে দিয়েছিল। যদিও লোকজন টের পেয়ে গরুটাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে। গো-ভূতেরা গরুকে সাধারণ আলের ধারেই পুতে ফেলতে চায়, তাই এদেরকে আল-চোরাও বলা হয়ে থাকে।
এই গো-ভুতের ব্যাখা নিয়ে মুরুব্বীদের সাথে তর্কও করেছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সব তর্ক বুমেরাং হয়ে আমার হৃদযন্ত্রে আঘাত করছে আর আমার রক্তস্রোত বেড়ে গিয়ে আমার ধমনিতে এমন তরঙ্গাভিঘাত সৃষ্টি করছে যেন আমি আমার রক্ত-তরঙ্গের শব্দ শুনতে পাচ্ছি এবং প্রত্যেকটি তরঙ্গ আমার কপালের দুপাশে হাতুড়িপেটা করছে।
দৌড়ে পালাবো, তারও উপায় নেই। কারণ, ভয় পেয়েছি, একবার যদি ভূতেরা বুঝতে পারে-তাহলে আর রক্ষে নেই। একেবারে পুতে ফেলবে। আর পিছন ফিরে তো দৌড় দেয়া যাবেই না। কারণ অশরীরী আত্মারা যত অনিষ্ট করে তা পিছন দিক থেকেই। পায়ে-পায়ে পিছিয়ে যাব, তারও উপায় নেই। কারণ পিছনে ঘন বাঁশঝাড়। ওর ভিতরে চাঁদের আলোও পড়ে না। আগেই বলেছি একেবারে নদীর ধার ঘেঁষে বেত, নাটা গাছের মত কাঁটা ঝোপ। পিছন ফিরে চলতে গেলে টলে নদীর ভিতরেই না পড়ি। তারপর গরমকালে দেখা গোখরো সাপের খোলসগুলোও চোখের সামনে এক ঝলক বিদ্যুতের মত চমকে গেলো। ওদিকে হাতের পাঞ্জাটি কেবল ইনিয়েবিনিয়ে ঘুরেফিরে নেচেনেচে আমাকে ডেকেই চলেছে।
এমন রুদ্ধশ্বাস ভৌতিক ভীতিকর পরিবেশে কতক্ষণ ছিলাম জানি না। পিছন থেকে টর্চের আলো পড়তেই সম্বিত ফিরে পেলাম। ভাড় ও বাঁক নিয়ে এসেছে আমার ছোটভাই। রাতের রস এখনই পেড়ে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তার আগে তার হাত থেকে টর্চ নিয়ে সেই ভৌতিক হাতের উপর আলোক সম্পাত করতেই কেমন যেন যাদুমন্ত্রবলে হাতটা একটা গাছে পরিণত হলো। আকন্দগাছ। শ্বেত আকন্দ। বসন্তের এলোমেলো বাতাসে আকন্দগাছের একটি পাতা ঘুরেফিরে একটা ছন্দে বাঁধাপড়ে দুলছে, কখনো এগুচ্ছে কখনো পিছিয়ে যাচ্ছে। জ্যোছনার আলো-আঁধারিতে আমার অনুধাবন শক্তি তাকে একটা দেহ-অবয়বহীন হাতের পাঞ্জা হিসেবে ভুল করেছে।